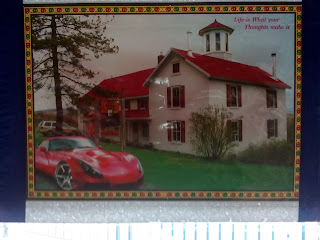(প্রথমেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নিই উইকিপিডিয়ার প্রতি, এছাড়াও আরও বেশ
কিছু ওয়েবসাইটের প্রতি যাঁদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এ লেখা রচিত।
নাম দিলে লেখা ভারাক্রান্ত হবে তাই আলাদা করে নামোল্লেখ না করার জন্য
সকলের কাছে মার্জনা চেয়ে নিলাম।)
দীপাবলি শব্দটির অর্থ প্রদীপসমূহ।
[সং. দীপ + আলি, আলী,..] অর্থাৎ প্রদীপের সমষ্টি। দীপাবলি – আলোর উৎসব। যে
উৎসব মনের অন্ধকার দূর করে মনকে স্বচ্ছ করে, অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে মানুষকে
দেখায় জ্ঞানের আলো। এই দিনে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন ভাবে এই
উৎসব পালিত হয়।
দীপাবলি ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, মরিশাস,
গুয়ানা, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, সুরিনাম, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও ফিজিতে
একটি সরকারি ছুটির দিন।
দীপাবলি বা দেওয়ালি উৎসবের কথা প্রথম পাওয়া
যায় পদ্ম পুরাণ ও স্কন্দ পুরাণে যা প্রথম সহস্রাব্দে লিখিত বলে অনুমান করা
হয়। স্কন্দ পুরাণে “দিয়া” কে সূর্যের যে আলো থেকে মানুষ তাঁর জীবন শক্তি
লাভ করে তার প্রতীক হিসাবে বোঝান হয়েছে। কার্তিক মাসে এই উৎসব পালিত হয়।
হিন্দুদের মধ্যে অনেকে এই উৎসবকে প্রথম খৃস্টপূর্বাব্দে রচিত কঠোপনিষদে
উল্লিখিত যম – নচিকেতা আখ্যানের সঙ্গে যুক্ত করেন। তাঁদের মতে কার্তিক
মাসে নচিকেতা যখন যমের বাড়িতে যান, তখন যম বাড়িতে ছিলেন না। নচিকেতা বিনা
জলপানে অভুক্ত এবং নিদ্রাহীন অবস্থায় যমের বাড়িতে তিনদিন – তিন রাত্রি
অপেক্ষা করেন। যম ফিরে এসে নচিকেতাকে যথেষ্ট সম্মান দিয়ে অভ্যর্থনা করেন
এবং তিনদিন অপেক্ষা করার প্রতিদানে নচিকেতা কে তিনটি বর দিতে সম্মত হন। এই
দিনটিতেই তিনি যমের কাছ থেকে সেই তিনটি বর প্রাপ্ত হন যার ফলে মানুষ ন্যায় –
অন্যায়, সত্য – অসত্য, প্রকৃত সুখ এবং সাময়িক আনন্দের মাঝে তুলনা করে সঠিক
পথে পরিচালিত হতে পারে। এক্ষেত্রে “দীপাবলি” শব্দের অর্থ হল জ্ঞানের আলো।
সপ্তম শতকে রাজা হর্ষবর্ধন তাঁর “নাগানন্দ” নাটকে “দীপাবলি” কে উল্লেখ
করেছেন “দীপাপ্রতিপদাউৎসব”Deepapratipadutsava (Deepa = light, pratipada =
first day, utsava = festival) নামে যেদিন প্রদীপ জ্বালানো হয় এবং নব
বিবাহিত দম্পতী কে উপহার দেওয়া হয়। গুর্জর প্রতিহার রাজ্যের রাজকবি
“রাজশেখর” (Rajashekhara) রচিত “কাব্যমীমাংসা” তে (যা কিনা ৮৮০ থেকে ৯২০
বছরের মধ্যে লিখিত) দীপাবলি উৎসব বর্ণনায় বলেছেন যে এই সময় বাড়ি – ঘর
পরিষ্কার করে নতুন করে রং করা হত এবং বাড়ি – ঘর ও রাস্তা আলো দিয়ে সাজানো
হত। প্রসিদ্ধ ফারসি ঐতিহাসিক ও পর্যটক আল বিরুনি একাদশ শতকে তাঁর ভারতবর্ষ
ভ্রমণ কালের বর্ণনায় জানিয়েছিলন যে ভারতীয় হিন্দুরা কার্তিক মাসের
অমাবস্যায় (New Moon Day) দীপাবলি উদযাপন করছে।
এছাড়াও উত্তর ভারতে
বসবাসকারী মানুষের (মূলত হিন্দি বলয়) এর এক বড় অংশ বিশ্বাস করেন ১৪ বছরে
বনবাস শেষ করে রাবণ হত্যাকারী রাম যখন সীতা, লক্ষণ ও হনুমান কে নিয়ে
অযোধ্যায় প্রবেশ করছিলেন তখন নগর বাসী তাকে স্বাগত জানানোর জন্য নিজেদের
বাড়ি – ঘর ও রাজপথ দীপমালায় সজ্জিত করেছিল। তার থেকেই দীপাবলি উৎসবের
প্রচলন। কিছু অংশের মতে পাণ্ডবরা এই দিনেই তাদের ১২ বছরের বনবাস এবং ১
বছরের অজ্ঞাতবাস শেষ করে জন সমক্ষে এসেছিলেন।
ভারতের উত্তর ও
পশ্চিম প্রান্তে ৫ দিনের দীপাবলি উৎসবের প্রথম দিন পালিত হয় “ধনতেরাস”। এই
দিনের আগে থেকে সেখানকার মানুষ তাঁদের বাড়ি ঘর, ব্যবসার জায়গা মেরামত করেন,
পরিষ্কার করে, সুন্দর করে সাজান। মহিলা ও শিশুরা ঘরের ভিতরে, ব্যবসার
জায়গায় এবং যাওয়া – আসার পথ ফুল – মালা দিয়ে সাজান, মেঝে সেজে ওঠে রঙ্গোলীর
রঙ্গে। পরিবারের অন্যরা ব্যস্ত থাকেন তার বাইরের আলোক সজ্জা ও অতিথি
আপ্যায়নের প্রস্ততিতে। (যে কথা না বললেই নয় - ভারতের অন্যতম প্রধান
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার শৈল্পিক একাত্মতা। ফুল ও রং দিয়ে তৈরি করা যে কারুকাজে
সেজে ওঠে বাড়ি – ঘর, পথের দু পাশ, উত্তর ও পশ্চিম প্রান্তের লোকেরা তাকে
বলেন “রঙ্গোলী”। সেই একই কাজ বাংলার মানুষের কাছে নাম নিয়েছে “আল্পনা”।
তামিলনাড়ুতে চলে যান দেখবেন নাম বদলে হয়ে গেছে “কোলাম”, রাজস্থানে ডাকে
“মণ্ডনা (Mandana) এবং আরও কত। পরে এ নিয়ে আলাদা করে কিছু লেখার ইচ্ছা
রইল।) ভারতের কিছু অংশের মানুষ “ধনতেরাস” এর দিনে সম্পদের দেবী লক্ষ্মী ও
চিকিৎসার দেবতা “Dhanvantari”র (দুঃখের বিষয় অনেক চেষ্টা করেও বাংলায় লিখতে
পারলাম না) জন্ম হয়েছে বলে বিশ্বাস করেন। এই দিনে বিশ্বাসী মানুষ সারা রাত
তাঁদের ঘরে প্রদীপ জ্বেলে এই দুই দেবতাকে শ্রদ্ধা জানান ও প্রার্থনা করেন
যে তাঁদের জীবন যেন সম্পদশালী ও নীরোগ হয়ে থাকে।
“ধনতেরাস” উৎসবের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, ভারতের উত্তর ও পশ্চিম প্রান্তের মানুষ কিছু না কিছু সোনা
– রুপোর গহনা বা অন্য কিছু জিনিস কিনে থাকেন। প্রথমে সম্পদের দেবী
লক্ষ্মীর আরাধনা, তারপর চলে বিক্রিবাটা। বর্তমানে বিভিন্ন ব্যবসায়ী এই সময়
বিক্রিত পণ্যের উপর বিশেষ ছাড় ঘোষণা করে থাকেন। প্রসঙ্গত, সময়ের সাথে সাথে
এই প্রথা আজ ভারতের অন্যান্য প্রান্তেও (বিশেষত পশ্চিম বাংলায়) বিস্তার লাভ
করেছে।
উৎসবের দ্বিতীয় দিন হল “নরক চতুর্দশী” যার অন্য আর একটি
নাম ছোটি দিওয়ালী। হিন্দুদের একটি অংশের বিশ্বাস, এই দিনে কৃষ্ণ, সত্যভামা ও
কালী তাঁদের মিলিত প্রচেষ্টায় নরকাসুরকে বধ করেছিলেন। তামিলনাড়ু, গোয়া ও
কর্ণাটকে এই দিনটিই “দিওয়ালি” হিসাবে পালিত হয়।
উৎসবের তৃতীয় দিন হল
সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা। মানুষের এক অংশের বিশ্বাস এই দিনে সম্পদের
দেবী লক্ষ্মী পৃথিবীতে নেমে আসেন। একই সাথে আরাধনা হয় গণেশ এবং কুবেরের। এই
একই বিশ্বাসে ভারতের পূর্ব প্রান্তের এক বড় অংশের মানুষ দুর্গা পূজার পরের
পূর্ণিমায় (কোজাগরী) দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা করেন। আবার, পশ্চিম বঙ্গের এক
বড় অংশের মানুষ (যারা এপার বাংলার লোক – চলতি কথায় ঘটি) এই একই বিশ্বাসে এই
দিন (অর্থাৎ উৎসবের তৃতীয় দিনে) অলক্ষ্মী বিদায় করে মহালক্ষ্মীর আগমনে
পূজার্চনা হয়। এইদিন বিশ্বাসী মানুষ, সম্পদের দেবীর আবাহনে সারারাত তাঁদের
ঘরের জানলা – দরজা খোলা রেখে তাতে প্রদীপ (দিয়া) জ্বালিয়ে রাখেন যাতে দেবী
লক্ষ্মীর আশীর্বাদ থেকে তাঁদের ঘর বঞ্চিত না হয়। বাড়ির চারপাশে জ্বলে
প্রদীপ, মানুষ একে অন্যের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন, করেন মিষ্টি বিতরণ।
এই উৎসবের দিনে বাচ্চা এবং বড়রা বিভিন্ন ধরনের আতসবাজিও ফাটিয়ে থাকেন।
চতুর্থ দিন। এই দিন মূলত স্বামী – স্ত্রীর মধ্যে মিলন বন্ধনের দিন। এই
দিনের নাম পাডয়া, বালিপ্রতিপদ (Padwa, Balipratipada) এই দিনে স্বামী –
স্ত্রী একে অন্যের সাথে উপহার বিনিময় করেন। ভারতের কিছু অংশে, এই দিনে
পরিবারের সদস্যরা প্রতীকী জুয়া খেলায় অংশ নেন। কিছু স্থানে বিবাহিতা বোনকে
তার দাদা / ভাই নিজে সঙ্গে করে বাপের বাড়ি নিয়ে আসেন।
পঞ্চম দিন।
ভাই দুজ। এ দিনের সৌন্দর্য বোধহয় ভারত ও নেপাল বাদে আর কোন দেশে নেই – কোন
দেশের মানুষ এভাবে ভাই – বোনের সম্পর্ক পালন করে না। নেপালে এই দিনটি পালিত
হয় “ভাই টিকা” নামে, এই দিনটি নেপালিদের অন্যতম প্রধান উৎসবের দিন। ভারতের
বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন নামে এই দিনটি পালিত হয় যেমন মহারাষ্ট্র, গোয়া ও
কর্ণাটকে ভাইফোঁটাকে বলে ভাইবিজ, তবে মূল অনুষ্ঠান একই থাকে।
এই
উৎসবের আরও একটি নাম হল যমদ্বিতীয়া। কথিত আছে, এই দিন মৃত্যুর দেবতা যম
তাঁর বোন যমুনার হাতে ফোঁটা নিয়েছিলেন। অন্য মতে, নরকাসুর নামে এক দৈত্যকে
বধ করার পর যখন কৃষ্ণ তাঁর বোন সুভদ্রার কাছে আসেন, তখন সুভদ্রা তাঁর
কপালে ফোঁটা দিয়ে তাঁকে মিষ্টি খেতে দেন। সেই থেকে ভাইফোঁটা উৎসবের প্রচলন
হয়। ভারতে যদিও এই অনুষ্ঠান মূলত ভাই – বোনকে নিয়েই তবুও এই অনুষ্ঠানের
আর এক মাধুর্য ফুটে ওঠে যখন ঠাকুমা / দিদিমা তাঁর নাতিকে ফোঁটা দেন বা বৌদি
ফোঁটা দেন তাঁর দেওরকে। বাঙালিরা এই উৎসবের নাম দিয়েছেন “ভাই ফোঁটা”।
বোনেরা ভাইদের কপালে ফোঁটা দেওয়ার সময়
“ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।
যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা, আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা॥
যমুনার হাতে ফোঁটা খেয়ে যম হল অমর।
আমার হাতে ফোঁটা খেয়ে আমার ভাই হোক অমর”
এই আশীর্বচন উচ্চারণ করে তাঁর / তাঁদের দীর্ঘ, নীরোগ জীবন কামনা করেন।
ভাই(রা) ও প্রণাম / আশীর্বাদের মাধ্যমে বোনেদের কল্যাণ কামনা করেন। তবে
পরিবার ভেদে এই ছড়াটির কিছু পরিবর্তন চোখে পড়ে।
এতো গেল “ধনতেরাস”
উৎসবের কথা। ভারতের পূর্ব প্রান্ত বাংলায় দীপাবলি দুভাবে পালন করা হয়, যার
কথা আগেই বলেছি। এছাড়া নরক চতুর্দশীর দিন বাংলার মানুষ উদযাপন করেন ভূত
চতুর্দশী নামে। এই দিনে চোদ্দ শাক খাওয়া এবং বাড়িতে চোদ্দ প্রদীপ জ্বালিয়ে
বাঙালি এই দিন পালন করে। বাঙালি মনে করে, ১৪ প্রদীপ জ্বালিয়ে তাঁর
পূর্ববর্তী চোদ্দ পুরুষকে আলোদান করে বর্তমান প্রজন্ম। লোককথায় এও শোনা
যায় যে এই প্রদীপসজ্জার মাধ্যমে পরিবারের পিতৃপুরুষদের অনুষ্ঠানে পদার্পণ
করার জন্য নিমন্ত্রণ পাঠানো হয়, যাতে তাঁরা মায়ের বাৎসরিক আগমনে উপস্থিত
হয়ে সবাইকে শুভাশীষ দিয়ে নিজেরা মায়ের আশীর্ব্বাদে মোক্ষ লাভ করবেন।
আমার ছোটবেলায় দেখেছি অনেক বাড়ির ছাদে পুরো কার্তিক মাস ধরে আকাশপ্রদীপ
জ্বলত। মানুষ মনে করতেন তাঁরা তাঁদের পিতৃ পুরুষের পথ আলোকিত করেছেন, যাতে
তাঁদের স্নেহাশিস থেকে পরবর্তী প্রজন্ম বঞ্চিত না হয়। সংখ্যায় কমে গেলেও
বহু বাড়ির ছাদে আকাশপ্রদীপ জ্বালানোর রীতি এখনও দেখা যায়। চোদ্দ শাক
খাওয়ার বিষয়টি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত। এই সময়ে মরসুম পাল্টায় | বাতাসে জায়গা
করে নেয় হিমেল পরশ | তাই শরীর ভাল রাখতে ১৪ রকম শাক খাওয়ার বিধি |
আসুন দেখে নিই এই শাকগুলো ( বা গাছের পাতা ) ঠিক কী কী --
১| ওল, ২| কেঁউ, ৩| বেতো, ৪| সর্ষে, ৫| কালকাসুন্দে, ৬| নিম, ৭|
জয়ন্তী, ৮| শাঞ্চে, ৯| হিলঞ্চ, ১০| পলতা, ১১| শৌলফ, ১২| গুলঞ্চ, ১৩|
ভাঁটপাতা, এবং ১৪| শুষণীশাক। বলা হয়, আয়ুর্বেদ এবং কবিরাজি শাস্ত্রে এইসব
শাকের গুণ অসীম।
বাংলায় কালী পূজা খুব প্রাচীন নয়। ১৭৭৭
খ্রিস্টাব্দে কাশীনাথ রচিত শ্যামাসপর্যাবিধিগ্রন্থে এই পূজার সর্বপ্রথম
উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে, নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অষ্টাদশ শতকে
তাঁর সকল প্রজাকে শাস্তির ভীতিপ্রদর্শন করে কালীপূজা করতে বাধ্য করেন। সেই
থেকে নদিয়ায় কালীপূজা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র
ঈশানচন্দ্রও বহু অর্থব্যয় করে কালীপূজার আয়োজন করতেন।পূর্ব বঙ্গের বাঙালী
হিন্দুরা কালীপূজার পরের প্রথমা তিথিতে (প্রতিপদ)ভাইফোঁটা উৎসব উদযাপন
করেন এবং এপার বাংলার মানুষ উদযাপন করেন দ্বিতীয়াতে। এই অনুষ্ঠানের বিষয়ে
পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।
এবার জানা যাক শিখ, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মের মানুষ কিভাবে এই দিন পালন করেন।
১৬১৯ খ্রিস্টাব্দে শিখদের ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ ও ৫২ জন রাজপুত্র দীপাবলির
দিন মুক্তি পেয়েছিলেন বলে শিখরাও এই দিন টিকে বন্দী ছোড় দিবস হিসাবে পালন
করেন।
জৈন মতে, ৫২৭ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে মহাবীর দীপাবলির দিনেই মোক্ষ
বা নির্বাণ লাভ করেছিলেন।তাই তাঁরা এই দিনকে “নির্বাণ দিবস” হিসাবে পালন
করে থাকেন।
আর্য সমাজ এই দিনে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর মৃত্যুদিন পালন করেন। তাঁরা এই দিনটি "শারদীয়া নব-শস্যেষ্টি" হিসেবেও পালন করেন।
বৌদ্ধ মতে এই দিন সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁরা এই দিনটিকে “অশোক বিজয় দশমী” রূপে পালন করে থাকেন।
নেপালের নিউয়ার বুদ্ধিস্ট যারা বিভিন্ন বজ্রযানী দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাঁরা এই দিনে লক্ষ্মী আরাধনা করে থাকেন।
তাহলে আমরা দেখতে পেলাম, “দীপাবলি” শুধু মাত্র হিন্দুদের উৎসব নয়
বৈচিত্রের মধ্যে যে ঐক্য মহাভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ তারই ধারামতে এ উৎসব আজ
মানুষের উৎসব। এই ঐতিহ্যকে নষ্ট করার, একে ভুলিয়ে দেওয়ার, এক বিশেষ ধারামতে
প্রবাহিত করার এক নির্মম – জঘন্য ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হচ্ছে বেশ কিছুদিন
ধরে। এই পদ্ম গোখরো গুলোর বিষে ভারতীয় সংস্কৃতির মৃত্যু যাতে না হয় –
আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যাতে সেই জ্ঞানের আলো সঞ্চারিত হয়, তাই এই
দীপাবলির প্রতিটি প্রদীপ থেকে জ্বলে উঠুক অজস্র মশাল আর সেই মশালের আগুনে
পুড়ে খাক হয়ে যাক পদ্ম গোখরোর বিষ।
আপাতত বিদায়। যারা ধৈর্য ধরে এ লেখা পড়লেন তাঁদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।
শ্রীতোষ ১৯/১০/২০১৭